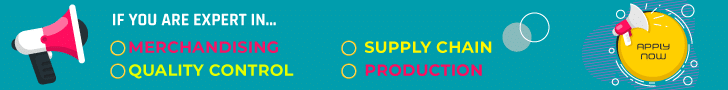স্বাধীনতা-পূর্ব ধনী বাঙালিদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিংবা কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা। উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের কেউই ধনী ছিলেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন নানা ধরনের ঠিকাদারি ব্যবসার মাধ্যমে তাদের উত্তরণ। সে সময় সংগৃহীত পুঁজি তারা বিনিয়োগ করেন মাঝারি ধরনের শিল্প-কারখানা, পরিবহন ব্যবসা, আমদানি-রফতানি ও জমি কেনাবেচায়। ষাটের দশকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেতে শুরু করেন তারা। এ পৃষ্ঠপোষকতাকে ভিত্তি করে পরবর্তীতে তারা বড় ধরনের উদ্যোগে বিনিয়োগ করেন। আর স্বাধীনতা-পরবর্তী চার দশকে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছে উল্লেখযোগ্য। মূলত বেসরকারি খাতই এতে ভূমিকা রেখেছে। অর্থনীতি বড় হওয়ার পাশাপাশি বেড়েছে সম্পদশালী পরিবারের সংখ্যাও।
১৯৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় অন্যতম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা পরিবার ছিল এ কে খান। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে শীর্ষস্থানে থাকলেও আশির দশকে এ কে খান পরিবারের স্থান ছিল পঞ্চম। বর্তমানে এ তালিকায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। বেসরকারি খাতে শীর্ষ ধনীর তালিকায় যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন নাম।
১৯৬৯-৭০ মেয়াদে শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হিসাব করা হয়েছে আনুমানিক সম্পত্তির ভিত্তিতে। এ তথ্য নিয়ে একটি তালিকা করেছেন গবেষক সের্গেই স্তেপানোভিচ বারানভ। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স প্রকাশিত মেম্বার ডিরেক্টরির তথ্য বিশ্লেষণ করে তৈরি হয়েছে ১৯৮৮ সালের শীর্ষস্থানীয় শিল্প ও বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর তালিকাটি। এ তালিকায় প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভারের উল্লেখ থাকলেও শীর্ষত্বের ভিত্তি সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। আর ২০১৩-১৪ করবর্ষের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিট সম্পদের ভিত্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য নিয়ে সর্বশেষ তালিকাটি তৈরি করেছে বণিক বার্তা।
যেকোনো দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি বেসরকারি খাত। সরকার এক্ষেত্রে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে বাংলাদেশের বেসরকারি উদ্যোক্তারা সুযোগ-সুবিধা খুব কম পেয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্য, ঘুষ আদান-প্রদান, অতি স্বল্প সেবা সুবিধা ও রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র এসব উদ্যোগকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। তার পরও বেসরকারি খাতের শীর্ষস্থানীয় উদ্যোক্তারা নিজস্ব সক্ষমতার জোরে এগিয়ে যাচ্ছেন। স্বাধীনতার আগে থেকে শুরু হওয়া এ ধারা এখনো অব্যাহত।
জানা গেছে, ১৯৬৯-৭০ মেয়াদে শীর্ষ ১০ বাংলাদেশী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা পরিবারের মধ্যে প্রথমেই ছিল এ কে খান পরিবার। এ পরিবারের প্রতিষ্ঠান ছিল ১২টি। সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক সাড়ে ৭ কোটি রুপি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা পরিবারটির নাম গুলবক্স ভুইয়া। এ পরিবারের প্রতিষ্ঠান ছিল পাঁচটি ও সম্পদের পরিমাণ সাড়ে ৬ কোটি রুপি। তৃতীয় স্থানে থাকা জহুরুল ইসলামের (ব্রাদার্স) প্রতিষ্ঠান ছিল ১৪টি ও সম্পদের পরিমাণ ৬ কোটি রুপি।
স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে চতুর্থ থেকে দশম স্থানে থাকা ধনী পরিবারগুলো ছিল যথাক্রমে মো. ফকির চাঁদ, মকবুল রহমান ও জহিরুল কাইউম, আলহাজ মুসলিমউদ্দিন, আলহাজ শামসুজ্জোহা, খান বাহাদুর মুজিবর রহমান, আফিলউদ্দিন আহমেদ এবং এমএ সাত্তার। পরিবারগুলোর অধীন প্রতিষ্ঠান ছিল যথাক্রমে নয়, ছয়, পাঁচ, চার, সাত ও পাঁচটি। এসব পরিবারের সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে ৬ কোটি, ৫ কোটি, ৫ কোটি, ৫ কোটি, সাড়ে ৪ কোটি, ৪ কোটি ও ৩ কোটি রুপি।
স্বাধীনতা যুদ্ধের পর একটি দরিদ্র, জনসংখ্যাধিক্যে জর্জরিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। শিল্প খাত, পুঁজিবাজার ও বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের উত্তরাধিকার বহন করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। ১৯৭৮-৭৯ পর্যন্তও মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ের মাথাপিছু আয় পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি বাংলাদেশ।
১৯৮২ সালে সরকার বাজারকেন্দ্রিক উন্নয়ননীতির পাশাপাশি একটি নতুন শিল্পনীতি গ্রহণ করে। এর আগে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এ নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে অংশীদার হয়। ১৯৮০ সালের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল খাদ্য ও কৃষি থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার, নির্বাচিত রাষ্ট্রমালিকানাধীন শিল্পের বেসরকারীকরণ, আংশিক আর্থিক উদারীকরণ ও আমদানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। আশির দশকের প্রথম ভাগে রাষ্ট্রমালিকানাধীন মোট ১ হাজার ৭৬টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়।
আশির দশকে জহুরুল ইসলাম গ্রুপ দেশের অন্যতম শীর্ষ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। মূলত ঠিকাদার ব্যবসার মাধ্যমে গ্রুপটি প্রতিষ্ঠা করেন জহুরুল ইসলাম। ১৯৮৮ সাল নাগাদ এ গ্রুপের বার্ষিক টার্নওভার দাঁড়ায় ৬২৮ কোটি টাকা। এ সময় গ্রুপের অধীন প্রতিষ্ঠান ছিল ২৪টি।
১৯৮৮ সালে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয়টি ছিল ইস্পাহানি। এমএম (সদরী) ইস্পাহানি প্রতিষ্ঠিত গ্রুপটির অধীনে ওই সময় কোম্পানি ছিল মোট ২৩টি। ১৯৪৭ সালেরও আগে প্রতিষ্ঠিত ইস্পাহানি স্বাধীনতা-পরবর্তীকালেও এ দেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ওই সময় কর্মচারীর সংখ্যা ২০ হাজার থেকে কমে ১২ হাজারে নামিয়ে আনে তারা। পরবর্তীতেও এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভাব ধরে রাখতে সক্ষম হয় পরিবারটি।
এএসএফ রহমান প্রতিষ্ঠিত বেক্সিমকো ছিল তালিকার তৃতীয় স্থানে। ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক টার্নওভার ছিল ৫২৪ কোটি টাকা। এর পরের স্থানে ছিল মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইনের আনোয়ার গ্রুপ। পঞ্চম স্থানে থাকা এ কে খান গ্রুপের টার্নওভার ছিল আশির দশকে ৪০০ কোটি টাকা। ওই সময় গ্রুপটির চেয়ারম্যান ছিলেন এএম জহিরুদ্দিন খান। ষষ্ঠ ধনী ব্যবসায়ী পরিবার ছিল মুহাম্মদ ভাই (প্যানথার)। এ তালিকায় পরের স্থানগুলোয় ছিল যথাক্রমে ডব্লিউ রহমান জুট, এপেক্স, প্যাসিফিক ও স্কয়ার গ্রুপ। ১৯৮৮ সালে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায়িত্বে পালন করেন যথাক্রমে লতিফুর রহমান, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, এম মোর্শেদ খান ও স্যামসন এইচ চৌধুরী।
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, সম্পদ বিবরণীর ভিত্তিতে ২০১৩-১৪ করবর্ষে দেশে ১০০ কোটি টাকার বেশি নিট সম্পদ রয়েছে, এমন ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫। তাদের মধ্যে নিট সম্পদে শীর্ষে রয়েছেন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী শওকত আলী চৌধুরী। তার প্রদর্শিত নিট সম্পদের পরিমাণ ২৭৫ কোটি টাকা। ফিনলে প্রপার্টির অংশীদার এ ব্যবসায়ী ইস্টার্ন ব্যাংকেরও পরিচালক। দ্বিতীয় সম্পদশালী ব্যক্তি নাভানা গ্রুপের সাইফুল ইসলাম, যার নিট সম্পদের পরিমাণ ২৭০ কোটি টাকা। এ তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বসুন্ধরা গ্রুপের সাদাত সোবহান। তার নিট সম্পদের পরিমাণ ২০৫ কোটি টাকা। ২০০ কোটি টাকা নিট সম্পদ নিয়ে তালিকার চতুর্থ স্থানে রয়েছেন হোসাফ গ্রুপের মোয়াজ্জেম হোসেন। তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছেন বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, যার নিট সম্পদের পরিমাণ ১৬৫ কোটি টাকা। শীর্ষ সম্পদশালীর তালিকায় এর পরের স্থানে রয়েছেন আফরোজা বেগম। তার নিট সম্পদের পরিমাণ ১৫৮ কোটি টাকা। ১৫৫ কোটি টাকা নিট সম্পদ নিয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছেন বসুন্ধরা পরিবারের আরেক সদস্য সাফওয়ান সোবহান। প্রাইম ব্যাংকের পরিচালক এমএ খালেক ও আকিজ পরিবারের দুই সদস্য সেখ বশির উদ্দিন ও সেখ জামিল উদ্দিনও রয়েছেন শীর্ষ দশের এ তালিকায়। তাদের প্রত্যেকেরই নিট সম্পদের পরিমাণ ১৪০ কোটি টাকা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন এ প্রসঙ্গে বণিক বার্তাকে বলেন, কালের বিবর্তনে পশ্চিমা দেশগুলোর শীর্ষ ব্যবসায়ীদের তথ্য পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সেখানে শীর্ষত্ব তৈরি হচ্ছে উদ্ভাবনের মাধ্যমে। মূলত প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী পণ্য বা সেবার ব্যবসা সেখানে গুরুত্ব পাচ্ছে। সাধারণ দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে পর্যবেক্ষণ তাতে দেখা যায়, এখানকার বেশির ভাগ ব্যবসায়ীই গতানুগতিক ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়েন। এর মধ্যেও অনেকে বড় আকারের ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ পান। এ সুযোগে যারা ব্যবসা বহুমুখী করেন, তারা দীর্ঘদিন টিকে থাকেন।