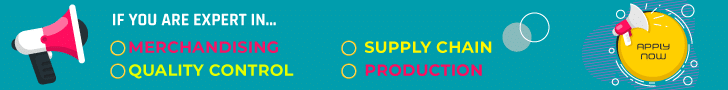টিনের শেডের নীচে খারাপ অবস্থায় তারা কল-কারখানায় কাজ করে। গণপরিবহনে বা দীর্ঘপথ হেঁটে তাদের দীর্ঘ দিনের শুরু হয়। বর্ষার বৃষ্টি বা গ্রীষ্মের তাপ তাদের সহ্য করতে হয়। তাদের অধিকাংশই কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও অল্প পরিমাণে উপার্জন করে এবং উপার্জনের অর্থে ঘর ভাড়া, খাবার, পোশাক এবং শিশুদের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় কঠিন হয়ে পড়ে।
অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা তাদের জন্য বড় কোনো স্বপ্ন। অবসর বলে যে কিছু আছে, সে সম্পর্কে খুব কমই জানেন তারা। কারণ প্রায় সবাইকে এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই ‘ওভারটাইম’ বেছে নিতে হয়। কারণ তাতেই তাদের জীবিকা অক্ষুণ্ণ থাকবে।
তাদের এই যান্ত্রিক জীবনে উপভোগের একমাত্র সময় ধর্মীয় উৎসবে প্রিয়জন ও পরিবারের সদস্যদের দেখতে পাওয়া। ব্যবস্থাপকদের কাছে কার্যত কোনো প্রতিনিধিত্ব না থাকায় যে আইনগুলো তাদের সুরক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছে সেগুলো মূলত তাদের ওপর তদারকি এবং নিয়োগকর্তাদের দয়ায় ন্যস্ত করা হয়। তাদের যখন নির্বিচারে ছাঁটাই করা হয়, তারা যখন কারখানায় দুর্ঘটনার শিকার হন বা বেকারত্বের মুখোমুখি হন, তখন তাদের রক্ষায় কোনো বীমা বা সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থাও নেই।
আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের শ্রমিকদের প্রায় প্রতিবাদহীন অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের পর তাদের প্রতিরোধহীনতা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি, বিশেষ করে মহামারি মোকাবিলায় আরোপিত কল্পিত লকডাউন দিন এনে দিন খাওয়া শ্রমিকদের কীভাবে প্রভাবিত করবে তা বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়েছে। অদক্ষ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যর্থতা সমাজে বসবাসকারী প্রান্তিক শ্রমিকদের ওপর অসমভাবে প্রভাব ফেলেছে।
গত ১০ আগস্ট একটি নাগরিক সংগঠনের আয়োজনে জনপরিসরের ভার্চুয়াল আলোচনায় ‘কোভিড ১৯ এবং শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা’ বিষয়ক আলোচনা হয়। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক ও নেতা। তৈরি পোশাক শিল্প, চা বাগান শিল্প, পর্যটন, হোটেল ও রেস্তোরাঁ শিল্প এবং রিকশাচালকসহ অন্যান্য খাতের শ্রমিক ও নেতারা এতে অংশ নেন।
আলোচনায় এ বিষয়ে কোনো ভিন্নমত ছিল না যে, দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভরশীলদের কোনো প্রকার সহায়তা না করেই লকডাউন সম্পর্কিত সরকারের সিদ্ধান্ত তাদের অনাহার, অপুষ্টি, দুর্বল স্বাস্থ্য ও ঋণগ্রস্ততাসহ অসহনীয় যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দিয়েছে।
তাড়াহুড়ো করে যে লকডাউনের সিদ্ধান্ত এবং তার সংশোধনী দেওয়া হয়েছিল, তা শ্রমিকদের ‘বিশৃঙ্খল, বিপজ্জনক, জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে ভ্রমণ করতে’ বাধ্য করেছিল।
লকডাউনের প্রথম দফায় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিল, কারখানার কাছাকাছি এলাকায় বাস করে এমন ৩০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কারখানা চালানো হবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন ছিল। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই কারখানা ব্যবস্থাপকরা গ্রামীণ এলাকায় অবস্থানরত কর্মীদেরও ফেরত এনেছিল। এই শ্রমিকরা চাকরি হারানোর ভয়ে অফিসে ফিরতে বাধ্য হয়েছিল। বলা বাহুল্য, পরিবহণ সুবিধা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রেখে তাদের ফিরতে বাধ্য করার কথা শ্রমিকদের মনে আছে।
দ্বিতীয় লকডাউনের সময় শ্রমিকদের কর্মস্থলে ফেরাতে পরিবহণ ১৬ ঘণ্টার জন্য পুনরায় চালু করার বিলম্বিত ও উদ্ভট সিদ্ধান্ত আবারও কর্তৃপক্ষের নির্লজ্জতা, অদক্ষতা এবং অসংবেদনশীলতার প্রতিফলন, যা শ্রমিকদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে।
গার্মেন্টস কর্মী প্যানেলিস্ট লকডাউনের পরিস্থিতিতে তার দুর্দশাপূর্ণ যাত্রার কথা বর্ণনা করে বলেন, ‘তারা প্রথম লকডাউন থেকে কিছুই শেখেনি এবং আমাদের আবারও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলেছে। তারা মনে করে আমরা যন্ত্র।’
যদিও কারখানা এবং রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের কর্মসূচিতে কল-কারখানাগুলোর প্রাধান্য শীর্ষে থাকা উচিত ছিল। কোয়ারেন্টিনসহ করোনা পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সেবায় সহজে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে এই ধরনের অগ্রাধিকার বাস্তবায়ন করা হয়নি। স্বাস্থ্যকর্মী, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের মতো সামনের সারিতে যারা রয়েছেন, তাদের করোনা টিকা প্রদানের কর্মসূচিকে ন্যায়সঙ্গতভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। তবে মহামারি চলাকালীন শক্তিশালী ব্যবসায়ী, সংস্থাসহ কেউই শ্রমিকদের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের শক্তি ব্যয় করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকার কথা বলেননি।
কারখানা প্রাঙ্গণে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরা অনেকাংশে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব হলেও শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করা একটি বড় সমস্যা। বেশ কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন কারখানায় ক্লাস্টার কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের ঝুঁকি তুলে ধরেছে। কাজ পুনরায় শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন কারখানায় সংক্রমণ বেড়েছে।
আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে, সাভারের বেশ কয়েকটি কারখানা করোনায় আক্রান্তদেরও কাজের অনুমতি দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা দাবি করেন, কেইসগুলো রিপোর্ট করার পরিবর্তে কারখানাগুলোর একটি অংশ চিহ্নিত করা হয়, যা সংক্রমণের ঘটনাগুলো চেপে যায়। যার ফলে সুস্থ শ্রমিকরা দুর্বল হয়ে পড়ে। ইউনিয়নের নেতারা শ্রমিকদের দাবি যাচাই করে বলেছিলেন, করোনায় আক্রান্ত হলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি, ভাতা, চিকিৎসা খরচ এবং ছুটির বিষয় উত্থাপন করা হয়। তবে, এগুলো কার্যকর করার নির্দেশিকার খসড়া এখনও তৈরি হয়নি। এটা হতাশাজনক যে, শীর্ষ বাণিজ্য সংস্থাগুলো এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সম্পৃক্ত না হয়ে উদাসীন থেকে গেছে।
কোভিড পরীক্ষাসহ আরও চেকআপের দায়িত্ব নেওয়ার পরিবর্তে, স্বাভাবিক তাপমাত্রার বেশি তাপমাত্রা শরীরে থাকা কর্মীদের বিনা বেতনে ছুটিতে পাঠানো হয়। সাভারের উলাইলে একটি গার্মেন্টস কারখানার ম্যানেজমেন্ট থেকে বেশ কয়েকজন ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক জবাব পান, ‘যদি ঘরে বসে থাকেন তাহলে বেতন কীভাবে চান?’ রপ্তানিমুখী শিল্পের মালিক পক্ষকে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা দেওয়া হয়েছিল। এই প্রণোদনায় শ্রমিকদের মজুরির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল।
অনুষ্ঠানের আলোচকরা দাবি করেন, করোনা মহামারির সময় যখন রাষ্ট্রের নির্বিচারে ছাঁটাই, মজুরি না দেওয়া এবং শ্রমিকদের শারীরিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে স্পষ্টতই নিষ্ক্রিয়তা ছিল, তখন বিভিন্ন কলকারখানায় অবস্থিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ‘অপ্রীতিকর ঘটনা’ এড়াতে নজরদারির ব্যাপারটি নিশ্চিত করে। এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের অসন্তোষের বৈধ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাদের ব্যাপকভাবে অবস্থান তৈরি করে।
শ্রমিক প্রতিনিধিরা দাবি করেন, ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে আশুলিয়ায় কমপক্ষে পাঁচ জন শ্রমিককে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ডেকে নিয়ে যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ‘উস্কানিমূলক পোস্ট’ দেওয়ার জন্য। তাদেরকে সারা দিন আটক রাখা হয়। পরবর্তীতে এমন পোস্ট করা থেকে বিরত থাকবে মর্মে বন্ডে সই নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
শ্রমিক প্রতিনিধিরা আরও দাবি করেন, অন্তত ছয়টি কারখানা অঞ্চলে কাল্পনিক মামলা দায়ের করা হয়েছে।
ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ সূত্রের দাবি, এপ্রিল মাসে ছয়টি অঞ্চলে ৪৪৪ জন শ্রমিক বিক্ষোভে অংশ নেন। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, কারখানা কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কয়েকজন শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।
চা শিল্পকে ‘খাদ্য’ হিসেবে অপরিহার্য খাত হিসেবে অভিহিত করেছে চা বোর্ড। ফলে, দেড় লাখ চা শ্রমিক মহামারির সময়ও দেশের ১৬৬টি চা বাগানে কাজ চালিয়ে যান (দ্য ডেইলি স্টার, ১২ এপ্রিল ২০২০)। একটি ইউনিয়নের নেতা দাবি করেন, ‘চা বাগান ভাইরাস মুক্ত।’ এই ধারণার পরেও বেশ কয়েকটি চা বাগানে করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর ফলে চা শ্রমিকদের ‘সাধারণ ছুটির’ আওতায় আনার দাবি ওঠে।
চা বাগানের দলগত কাজে শ্রমিকদের কাছাকাছি থাকা প্রয়োজন হয়, যা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায় (দ্য ডেইলি স্টার, ১ মে ২০২০)। কর্মস্থলে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট না থাকা এবং হাতের তালু ব্যবহার করে পানি পান করার ব্যবস্থাও ঝুঁকি বাড়ায়। মহামারি চলাকালীন মজুরি না পাওয়া চা শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে কুলাউড়ায় প্ল্যাকার্ড এবং খালি থালা নিয়ে দুই ঘণ্টার ‘ক্ষুধার্ত লংমার্চ’ করতে বাধ্য হয়।
মহামারির বিরূপ প্রভাবে (প্রভাব?) পর্যটন, হোটেল ও রেস্তোরাঁ শিল্পেও লাখো শ্রমিককে কাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাদের অনেকেই কুলি, রিকশাচালক এবং সবজি বিক্রেতা হয়েছেন। তারা সরকারি কর্তৃপক্ষের থেকে কোনো প্রকার সুবিধাদি পাননি।
পরিবহণ খাতের কর্মীরাও মহামারির সময় বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। অনাহারের দ্বারপ্রান্তে ছিল অনেক পরিবার। এটি বিশেষভাবে হতাশাজনক যে, প্রায় ৭০ লাখ পরিবহণ শ্রমিকের কাছ থেকে সংগঠন পরিচালনা ব্যয় ও শ্রমিক কল্যাণের নামে স্বাভাবিক সময়ে বছরে অন্তত দুই হাজার কোটি টাকা চাঁদাবাজি হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই ধারণা সড়ক পরিবহণ খাতের বিভিন্ন পক্ষের হিসাবে। অভিযোগ এসেছে, ফেডারেশন ইউনিয়নগুলোর নেতারা সরকারি সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে ‘তালিকার রাজনীতি’ করছে।
একই অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে রিকশা চালকদেরও। রিকশা চালকরা ‘অসমভাবে’ লকডাউন প্রয়োগের ভুক্তভোগী। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর রিকশা চালকদের প্রতি অবমাননাকর আচরণ এবং রিকশা জব্দ করার প্রচুর খবর ও প্রতিবেদন রয়েছে। ব্যাটারিচালিত রিকশা নিষিদ্ধ করার সময়সীমার ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত এই মহামারির সময় ৬০ লাখ পরিবারকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। শ্রমিকদের বহন করতে হয়েছে বিশাল সামাজিক খরচও। অনেক শ্রমিক পরিবার আয়ের উৎস হারিয়ে সন্তানদের স্কুল না দিয়ে পাঠিয়েছেন কাজে। অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সংসারের খরচ কমানোর কৌশল হিসেবে।
আলোচকরা মনে করেন, সরকারের সময় এসেছে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া, বীমা ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা এবং স্বাস্থ্যসেবা চাহিদাকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেওয়ার।
তারা আরও দাবি করেন, শ্রমিকদের টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে যেন অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং মহামারি চলাকালীন তাদের ঝুঁকি ও পরিবহণ ভাতা দেওয়া হয়। শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত প্রণয়নে শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরা হয়।
নাগরিক ওয়েবিনার মহামারি চলাকালীন দেশের উন্নয়নের প্রধান কারিগর লাখো শ্রমিকের যাপিত অভিজ্ঞতার ওপর আলোকপাত করে। এখন সময় এসেছে নীতিনির্ধারকদের বহুল আলোচিত জাতীয় উন্নয়নের বিপরীত দিকটিও বিবেচনা করার এবং এটা নিশ্চিত করা যে, শ্রমিকরা তাদের অধিকার, স্বীকৃতি ও মর্যাদা পাচ্ছে। তদুপরি প্রয়োজন করোনা মহামারির সময় জীবন-জীবিকার বিপরীতে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার।
সি আর আবরার ও আনু মুহাম্মদ শিক্ষক, জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী এবং রেজাউর রহমান লেনিন একজন অ্যাকাডেমিক অ্যাক্টিভিস্ট।
(দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, দ্য ডেইলি স্টার কর্তৃপক্ষের নয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো প্রকার দায়ভার দ্য ডেইলি স্টার নিবে না।)