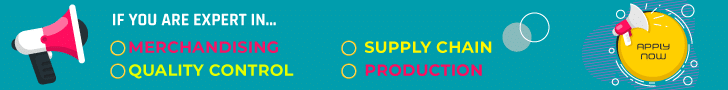ভুল
নীতির কারণে দেশের সম্ভাবনাময় বস্ত্র খাত এখন ধ্বংসের
দ্বারপ্রান্তে। বিশেষ করে ওভেন সেক্টরকে বিপদের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে।
যার দায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো কোনোভাবে এড়াতে পারে না।
প্রয়োজন ছিল, পর্যায়ক্রমে গার্মেন্টের জন্য কাপড় আমদানি কমিয়ে দেশের অভ্যন্তরে
স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে তোলা।
এছাড়া
প্রণোদনা দেয়াসহ মনিটরিং বডি গঠন করে যা যা করার দরকার ছিল, তা এ পর্যন্ত
কোনো সরকারই করেনি। বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী নেতারা নিজেদের আখের
গোছাতে ব্যস্ত। এই শিল্পের স্বার্থে শক্ত অবস্থান না নিয়ে কীভাবে সরকারের
চাটুকারিতা করে বড় বড় সুবিধা আদায় করা যায়, রাজনৈতিক পদপদবি পাওয়া যায়, বন্ডের সুতা ও
কাপড় এনে কালোবাজারে বিক্রি করে রাতারাতি কোটি কোটি টাকার মালিক
হওয়া যায়- তারা ব্যক্তিস্বার্থে এসব পথেই হেঁটেছেন।
ফলে যা
হওয়ার, তা-ই
হয়েছে। এখন চীন থেকে কাপড় আমদানি আরও বিলম্বিত হলে শুধু
গার্মেন্ট খাত নয়, এর সঙ্গে ব্যাংকসহ আরও অনেক খাত ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু
এই সংকট নিয়ে অন্য কাউকে দোষারোপ করে লাভ নেই।
এই
পরিস্থিতির জন্য আমরা কে কতখানি দায়ী, সেটিই আজ বিচার-বিবেচ্য বিষয়। সূক্ষ্মভাবে
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ভুল নীতির কারণে যে ক্ষতি হচ্ছে, তার মাশুল
প্রকারান্তরে রাষ্ট্রকেই দিতে হচ্ছে। সৃষ্ট সংকট নিয়ে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীদের
অনেকে সোমবার যুগান্তরের কাছে ক্ষোভ-অসন্তোষ প্রকাশ করে এমন তির্যক মন্তব্য
করেন।
তারা
বলেন, সুতায়
নেই আমদানি ঠেকানো প্রটেকশন। বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ওভেনে
দেয়া হচ্ছে না প্রণোদনা। এছাড়া গার্মেন্টগুলোকে দেশীয় কাপড় কেনার
ক্ষেত্রে বেঁধে দেয়া হয়নি কোনো সিলিং। শুধু সরকারের এসব ভুল নীতির কারণে
শত শত সুতা ও কাপড়ের মিলগুলো শুরু থেকে নানামুখী সংকট মোকাবেলা করে আসছে।
এখন করোনাভাইরাসের কারণে বড় ধরনের কাপড় সংকটে পড়েছে গার্মেন্ট সেক্টর।
সময়
থাকতে যদি কাপড়ের মিলগুলোকে প্রয়োজনীয় নীতিসহায়তা দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ
করা হতো, তাহলে আজ চীনের কাপড়ের জন্য গার্মেন্টগুলোকে বসে থাকতে
হতো না। অথচ করোনাভাইরাসের প্রভাব দীর্ঘায়িত হলে বেশির ভাগ গার্মেন্টে
উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। বিশ্লেষকদের অনেকে এমন পূর্বাভাস দিচ্ছেন, যা নিয়ে এখন
সরকারের নীতিনির্ধারক মহলসহ সংশ্লিষ্ট সবাই উদ্বিগ্ন।
কিন্তু
এই শেষ সময়ে উদ্বিগ্ন কিংবা প্রকৃত তথ্য গোপন করেও লাভ নেই। বাস্তব সংকট
সবাইকে মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? ৩০ বছর ধরে সব সরকার একশ্রেণির নেতিবাচক আমলাদের ফাঁদে পা দিয়ে সঠিক নীতি প্রণয়ন
করতে পারেনি। বাস্তব অবস্থা না বুঝে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত নীতিনির্ধারক
মহল ভুলপথে হেঁটেছেন।
ফলে
সেভাবে কোমর সোজা করে দাঁড়াতেই পারেনি খুবই সম্ভাবনাময় এই সেক্টর। তারা
বলেন, প্রণোদনা
বহাল রাখাসহ বেশি সুবিধা দেয়ার কথা ছিল সুতা ও কাপড়ের মিলে। কিন্তু
সরকার দিয়েছে শুধু গার্মেন্টে। যারা শুধু সেলাইয়ের কাজ করে। দর্জিগিরি
বললে অনেকে আবার ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু এটিই তো বাস্তবতা।
এই
খাতের রফতানি আয় দেখিয়ে বাহবা নেয়া হচ্ছে। যদিও গোপন করা হয় প্রকৃত রফতানি
আয়। মোট রফতানি আয় থেকে ব্যাক টু ব্যাক এলসির হিসাব বাদ দেয়া হয় না। বিপরীতে
নব্বইয়ের দশকে স্পিনিং খাতে দেয়া ২৫ শতাংশ প্রণোদনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে
আনা হয়েছে।
বিকেএমইএ’র
প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম যুগান্তরকে বলেন,
ওভেন খাতে ব্যাকওয়ার্ড
লিংকেজ শিল্প গড়ে উঠেনি পর্যাপ্ত নীতিসহায়তার অভাবে। এর পেছনে ব্যবসায়ী
নেতাদের ভূমিকা আছে। মোদ্দা কথা, বস্ত্র খাতের সব সংগঠন এক হয়ে সমস্যাগুলো
সরকারের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেনি।
তিনি
মনে করেন, ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের উন্নয়নে মনিটরিং বডি গঠন করা দরকার
ছিল শুরুতেই। যার কাজ হবে পর্যায়ক্রমে আমদানি কমিয়ে এনে দেশের অভ্যন্তরে
ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ বাড়ানো। এছাড়া প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রাখা, যা আমাদের
প্রতিযোগী দেশগুলো করছে।
তিনি
আরও বলেন, নিট খাতে সহায়তা দেয়ায় এখন ৮৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন হচ্ছে। ওভেন
খাতে বড় বিনিয়োগ দরকার। আর ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ দিয়ে ওভেন খাতের ব্যাকওয়ার্ড
লিংকেজ শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব না। সরকারের উচিত হবে,
ওভেন খাতে বিশেষ
প্রণোদনা দিয়ে এই সেক্টরের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।
বিশ্বব্যাংকের
সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, গার্মেন্ট
খাতের শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প দেশে গড়ে উঠলে এই সময়ে
ব্যবসায়ীদের এত চিন্তিত হতে হতো না। কিন্তু সেটি না থাকায় এখন উৎপাদন বন্ধের
আশঙ্কায় রয়েছেন অনেকে। দেশে ব্যাকওয়ার্ড শিল্প তথা সামগ্রিক পোশাক খাতের
উন্নয়নে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মনিটরিং কমিটি গঠন করা উচিত। যে কমিটির
কিছু দাঁত থাকবে, মানে কমিটির দেয়া শিল্পের উন্নয়ন ও ব্যবসাবন্ধব পরিবেশ
সুপারিশ আমলে নিয়ে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।
এ
খাতের বিশেষজ্ঞদের কয়েকজন নাম প্রকাশ না করে প্রতিবেদককে বলেন, একটি গার্মেন্ট
স্থাপন করতে খরচ হয় ১৫-২০ কোটি টাকা। অথচ ওই গার্মেন্টের বিপরীতে ব্যাংক
থেকে তুলে নেয়া হয় ৫শ’ কোটি টাকার ঋণ। যা নানা পন্থায় বিদেশে অনেকে পাচার
করে থাকেন। একপর্যায়ে কেউ কেউ ব্যাংকের টাকা মেরে দিয়ে প্রতিষ্ঠানে তালা
ঝুলিয়ে দেয়। অথচ সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে গার্মেন্টের জন্য।
অন্যদিকে
ভালো মানের একটি ওভেন মিল স্থাপন করতে ব্যয় হয় কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা, যা এক বিশাল
কর্মযজ্ঞ। যেখানে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়। কিন্তু
দুর্ভাগ্য, ওভেনের জন্য সরকারের নীতিসহায়তা শূন্য। অথচ ওভেন ফ্যাক্টরি
স্থাপনের পর উদ্যোক্তাকে একদিকে ব্যাংক ঋণের বিপরীতে উচ্চ সুদ হারের
বোঝা টানতে হয়, অপরদিকে কম দামে ফেব্রিক্স বিক্রি করতে হয়।
কারণ, যেসব দেশ থেকে
সবকিছু আমদানি করে তিনি কাপড় তৈরি করছেন, সরকার ওইসব দেশের সঙ্গে তাকে বাজার প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিচ্ছে।
এখানে সরকারের কোনো প্রটেকশন নেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রয়োজন ছিল-
সরকার এখানে বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার রেশিও হিসাব করে একদিকে যেমন ওভেন
মিল মালিকদের ভর্তুকি দেবে, তেমনি ৩-৪% সুদে ঋণ দেবে।
এছাড়া
চালু হওয়া একটি ওভেন মিলকে কমপক্ষে ৭ বছর ১৫% হারে ভর্তুকি বা প্রণোদনা
দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, এটি হবে বিশেষ ব্যবস্থা। এভাবে নীতিমালা প্রণয়ন
করতে হবে। পৃথিবীর যেসব দেশ এসব সেক্টরে উন্নতি করেছে, তারা এভাবে শুরু
করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে।
দুর্ভাগ্য
হল, আমাদের
দেশে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি নিয়ে কেউ কখনও ভাবেনি। দেখা গেছে, যেখানে বিনিয়োগ
কম, সব
মনোযোগ সেখানেই দেয়া হয়েছে। ফলে আজ সুতা ও কাপড়ের মিলে হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ ঝুঁকির মুখে।
একদিকে উচ্চ সুদের ফাঁদ, অপরদিকে উৎপাদন করেও বাজারে টিকে থাকতে না পারার যন্ত্রণা
মিল মালিকদের কুরে কুরে খাচ্ছে। একসময় দেখা যাবে, বন্ধের
সাইনবোর্ড ঝুলছে।
বাংলাদেশ
টেক্সটাইল মিল অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন বলেন, কিছু অজ্ঞ লোক
সরকারকে ভুল বোঝানোর কারণে দেশের ওভেন খাতের ব্যাকওয়ার্ড
লিংকেজ শিল্প গড়ে উঠছে না। যদি দেশে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ে
উঠত, তাহলে
আমাদের চীনের কাছে ধরনা দিতে হতো না।
দেশের
টেক্সটাইল খাতই ওভেন কাপড়ের চাহিদা মেটাতে পারত। কিন্তু দেশের সুতা ও
কাপড়ের মিলকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে যেসব পদক্ষেপ নেয়া দরকার ছিল, তা ৩০
বছরে কোনো সরকারই নেয়নি।
তিনি
আরও বলেন, একশ্রেণির আমলা ও ব্যবসায়ী সরকারকে বোঝাতে চায়, তুলা আমদানিনির্ভর
হওয়ায় দেশে টেক্সটাইল শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এটা ডাহা মিথ্যা কথা।
জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান একসময়
ফেব্রিক্সে লিড দিত। ওইসব দেশে কি তুলা উৎপাদন হতো? হতো না। আবার আফ্রিকা ও উজবেকিস্তানে তুলা উৎপাদন হয়, সেখানে কি
টেক্সটাইল শিল্প গড়ে উঠেছে? তিনি বলেন, ‘বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা
করেছি, কিন্তু
ফল পাইনি। কারণ, ওই শ্রেণির আমলা ও একটি চক্র সব সময় তাদের
স্বার্থে সরকারকে ভুল বোঝায়।
সংশ্লিষ্টরা
জানান, উচিত
ছিল আমদানির ক্ষেত্রে শুরু থেকে দেশীয় সুতা ও কাপড় ব্যবহারে
কোটা নির্ধারণ করে দেয়া। প্রতিবছর ৫ শতাংশ করে বাড়ালে আজ বাংলাদেশ
বস্ত্র খাতে শতভাগ ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের সক্ষমতা অর্জন করতে পারত। বস্ত্র
খাতের কয়েকজন উদ্যোক্তা যুগান্তরকে বলেন, রফতানিমুখী একটি কাপড়ের মিল করেও আমরা
দেশে বিক্রি করতে পারছি না। প্রশ্ন হল- একটি মিল চালু করার প্রথমদিন থেকে
কি শতভাগ কোয়ালিটি সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব।
এটি
কোনো দেশেই সম্ভব না। সবদিক থেকে ১০০% কোয়ালিটি কাপড় তৈরি করতে ২ থেকে ৩
বছর লেগে যায়। তাহলে ওই মানে উন্নীত করতে গিয়ে যত কাপড় রফতানি থেকে বাদ
পড়বে, সেগুলোর
কী হবে। এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হবে, রফতানি ক্যাটাগরিতে যেসব কাপড় বাদ পড়বে, সেগুলো দেশের বাজারে বিক্রির অবাধ সুযোগ করে দেয়া। তাহলে
মিলগুলো ক্ষতি পুষিয়ে দ্রুত সক্ষমতার দিকে এগিয়ে যাবে।
অপরদিকে
গার্মেন্টগুলোকে তাদের আমদানি চাহিদার অন্তত ৩০ শতাংশ কাপড় দেশের মিলগুলো
থেকে কেনা বাধ্যতামূলক করে দিতে হবে। আমদানি মূল্যের চেয়ে দাম বেশি হলে
সরকার উৎপাদককে প্রয়োজনীয় নগদ সহায়তা দিয়ে দাম সমন্বয় করবে। এতে দেখা যাবে, চীন ও ভারত
যদি মিটারপ্রতি ২ ডলারে দেয়, সেখানে স্থানীয় মিলগুলো থেকে একই কাপড় তারা দেড় ডলারে কিনতে পারবে।
ফলে
প্রতিবছর স্থানীয় মিলগুলোর একদিকে যেমন উৎপাদন সক্ষমতা বাড়বে, তেমনি কাপড়ের
গুণগত মানও দিন দিন বাড়তে থাকবে। উদ্যোক্তারা বলেন,
মূলত সরকারের পলিসি
বা নীতি হতে হবে এ রকম, যা সব দেশ করে থাকে। চীন,
ভারত, পাকিস্তানসহ যেসব
দেশ ইতিমধ্যে বস্ত্র খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, তাদের সরকারগুলো
শুরু থেকে এভাবে সহায়তা দিয়ে আসছে। এমনকি চীন এখন পর্যন্ত তাদের শিল্পোদ্যোক্তাদের
সেক্টর বিবেচনায় ১২ থেকে ১৭ শতাংশ পর্যন্ত প্রণোদনা দিয়ে আসছে।
কিন্তু
এখানে সে সুযোগ নেই। ১৯৯০ সালের দিকে যখন দেশে সুতার মিলের যাত্রা শুরু
হয়, তখন
সরকারের পক্ষ থেকে ২৫ শতাংশ প্রণোদনা সুবিধা দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে
সেটি কমাতে কামতে একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এভাবে প্রণোদনা
দেয়ার কারণে সেসময় বহু মিল গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আসল কাজ না
করে উল্টো প্রণোদনা বন্ধ করে দেয়া হয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, সুতার মিলে এখন
সবচেয়ে বেশি দরকার হল- আমদানিতে শতভাগ প্রটেকশন দেয়া।
অর্থাৎ
অবৈধভাবে সুতা আসা ঠেকানোর পাশাপাশি বৈধ পন্থায় সুতার আমদানিও বন্ধ
করতে হবে। তাহলে সঙ্গতকারণে দেশীয় সুতার চাহিদা ও বিক্রি বাড়বে। এভাবে এসব
মিল শক্ত অবস্থানে চলে আসবে। কিন্তু এখানে সুতা আমদানি উন্মুক্ত করা ছাড়াও
প্রতিদিন চোরাই পথে দেদার সুতার চালান ঢুকছে। এছাড়া বন্ডের সুতায় বাজার
তো সয়লাব। এই যখন অবস্থা, তখন সুতার মিল দাঁড়াবে কীভাবে।
এদিকে
উৎপাদনে থাকা সুতা ও ওভেন মিলগুলোকে পদে পদে আমলাতান্ত্রিক হেনস্তার
শিকার হতে হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কোনো নথি
গেলে এমন আচরণ করা হয়, যেন উদ্যোক্তারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান করে বড় অপরাধ করে
ফেলেছেন। বস্ত্র খাতে রফতানি পর্যায়ে এখন যে ৫ শতাংশ প্রণোদনা দেয়া হয়, তা পেতে বছরের
পর বছর চরকির মতো ঘুরতে হয়। অথচ উচিত ছিল, উৎপাদন পর্যায়ে কমপক্ষে ১৫ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান নিশ্চিত করাসহ সব ধরনের
বাধা দূর করা।
এফবিসিসিআই’র
সহসভাপতি ও বিজিএমইএ’র সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, চীনের
করোনাভাইরাসের কারণে দেশের গার্মেন্ট খাত এখন বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। এর
কারণ, ওভেন
খাতে পর্যাপ্ত ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ে না ওঠায় এখনও ৭০ শতাংশের
বেশি কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। দেশে কিছু টেক্সটাইল গড়ে
উঠলেও সেগুলো চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারছে না।
কারণ, দেশে উৎপাদিত
ফেব্রিক্সের দাম কিছুটা বেশি। উপরন্তু, ব্যাংক ঋণের এত উচ্চ সুদ দিয়ে প্রতিযোগী সক্ষমতা গড়ে তোলা সম্ভবও নয়।
এজন্য দেশি ওভেন ফেব্রিক্স উৎপাদনে সরকারকে ভর্তুকি দেয়া উচিত। এতে সরকারের
লাভ হবে। কারণ একদিকে কর্মসংস্থান বাড়বে,
অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়
হবে।
প্রসঙ্গত, এখানে একটি
সুতা কিংবা কাপড়ের মিল করতে গেলে মেশিনারিজ, কাঁচামাল, বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল চীন,
ভারত কিংবা ইউরোপের কোনো দেশ
থেকে আমদারি করতে হয়। এমনকি মিল চালানোর জন্য টেকনিক্যাল লোকজনও
মোটা অঙ্কের বেতন দিয়ে ওইসব দেশ থেকে আনতে হয়। আবার পণ্য উৎপাদন করার পর
বিক্রির সময় প্রতিযোগিতা করতে হয় উল্লিখিত দেশের পণ্যের সঙ্গে।
প্রশ্ন
হল- এটি কি আদৌ সম্ভব? কেননা, চীন, ভারত যে দামে সুতা ও কাপড় দিতে পারবে, বাংলাদেশের
মিল মালিকরা তা কখনও পারবে না। মূলত এখানেই হল সরকারের আসল
ভূমিকা রাখার বিষয়। দেশকে যদি শিল্প ও শিল্পের কাঁচামালে স্বয়ংসম্পূর্ণ
করতে হয়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর পলিসি গ্রহণ করতে হবে।
বিশ্লেষকরা
বলেন, এখানে
সরকারের মূলত করণীয় বিষয় তিনটি। যেমন- প্রথমত, উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দিয়ে কাপড়ের দামের
পার্থক্য কমিয়ে আনা। যাতে আমদানি দরের চেয়ে স্থানীয় মিল মালিকরা কম দামে বিক্রি
করতে পারেন, সেজন্য সমহারে নগদ সহায়তা দেয়া। দ্বিতীয়ত, গার্মেন্ট
মালিকদের আমদানি চাহিদার নির্ধারিত পরিমাণ কাপড় স্থানীয় মিল থেকে কিনতে
বাধ্য করা।
তৃতীয়ত, প্রণোদনা প্রদান
ও নির্ধারিত কোটায় কাপড় বিক্রি নিশ্চিত করতে প্রতিবছর যাতে
ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ বাড়ে, সেজন্য শক্ত মনিটরিং অথরিটি গঠন। গঠিত মনিটরিং
অথরিটিকে স্থানীয় ওভেন মিলগুলোর বার্ষিক গড় উৎপাদন সক্ষমতা হিসাব করে সে
অনুযায়ী গার্মেন্ট মালিকদের আমদানির ওপর সিলিং নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ
দেশে যে পরিমাণ কাপড় উৎপাদিত হবে, সে পরিমাণ কাপড় তারা আমদানি করতে পারবে
না। এভাবে টানা ১০ বছর করতে পারলে দেশের বস্ত্র খাত গুণে ও মানে সবদিক
থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে।
প্রশ্ন
উঠতে পারে, সরকার কেন এ ধরনের নীতিসহায়তা দেবে। সহজ উত্তর- সরকারের
নীতিনির্ধারকরা প্রণোদনা সহায়তার অর্থ তো নিজেদের ঘর থেকে এনে দেবে না।
জনগণের ট্যাক্সের পয়সা থেকে দেবে। বিনিময়ে জনগণ এর কয়েকগুণ বেশি ফেরত পাবে।
কারণ এই সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লাখ লাখ বেকারের চাকরি হবে। আমদানি
কমে গেলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। সফল ও ভালো সরকারের কাজ- এভাবে বাস্তব
অবস্থা বুঝে নীতিসহায়তা দেয়া।
স্বাভাবিকভাবে
প্রশ্ন উঠতে পারে- তাহলে আমাদের সরকারের নীতিনির্ধারক মহল সহজ এই বিষয়টি
কি জানেন না। কিন্তু না জানার তো কোনো কারণ নেই। সমস্যাটা হল- তারা যখন
বাজারে শাড়ি কাপড়ের দোকানে যান, তখন বিদেশি কাপড় তালাশ করেন বেশি বেশি।
এ
কারণে প্রতিটি কাপড়ের দোকানে আমদানি ও চোরাইপথে আনা বিদেশি কাপড়ে ঠাসা।
খোদ রাজধানীর মধ্যে বিশাল কাপড়ের মার্কেট বলে খ্যাত ইসলামপুর মার্কেটে কী
বিক্রি হয়, সে বিষয়ে সরকারের নীতিনির্ধারক মহল কখনও খোঁজ নিয়ে দেখেছেন? এটি আসলে
বন্ডের নামে বিনা শুল্কে আনা বিদেশি কাপড়ের রমরমা বাজার। তাহলে
দেশীয় কাপড়ের গতি কীভাবে হবে?
বিশ্লেষকরা
মনে করেন, সরকারে যারা আছেন, তাদেরকে আগে গোল নির্ধারণ করতে হবে। তারা কি
দেশীয় কাপড়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চান। যদি চান, তাহলে সেক্ষেত্রে যা যা করা দরকার,
সেটি এখনই করতে হবে। এমনিতে
দিনে দিনে বেলা অনেকদূর গড়িয়েছে।
বলা
যায়, সময় আর
হাতে খুব বেশি নেই। করোনাভাইরাস জোরেশোরে আঘাত হানলে এবং
দীর্ঘস্থায়ী হলে শুধু গার্মেন্ট সেক্টর নয়, পুরো বস্ত্র খাত গভীর সংকটে পড়বে। অথচ আজ
যদি গার্মেন্ট খাত দেশীয় সুতা ও কাপড় ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জন করতে পারত, তাহলে আমদানির
জন্য নতুন বাজার তালাশ করতে হতো না।
বেসরকারি
গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক ড.
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, সব দেশেরই ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প তার
সামর্থ্যরে প্রমাণ করে। নিট খাতে শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প
গড়ে ওঠায় ভালো দাম পাচ্ছি।
কিন্তু
ওভেন খাতে অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। কারণ ওভেন খাতে সেভাবে
ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ে ওঠেনি। পর্যাপ্ত নীতিসহায়তা গ্রহণ করতে
না পারায় এটি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশের স্বার্থেই ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প
গড়ে তুলতে সরকারের নীতিসহায়তা দেয়া দরকার।
এখনও
সেই সুযোগ আছে। ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের ভবিষ্যৎ আছে। দেশে ওভেন ফেব্রিক্স
উৎপাদন করা গেলে রফতানির লিড টাইম কমে আসবে। সর্বোপরি সরকারকে শিল্পের
কথা মাথায় রেখে একটি সমন্বিত নীতি প্রণয়ন করতে হবে।